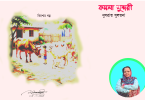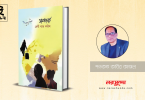কার্তিক মাস প্রায় শেষ হয়ে এলো। এ সময় প্রায়ই বৃষ্টি হলেও এখন বৃষ্টি নেই। মেঘের ওড়াউড়ি বা দাপাদাপি নেই। কিন্তু সুর্যোদয়ের সাথে সাথে রোদের তাপ বাড়তে থাকে ধীরে। যেমন করে পেটে চিনিচিনিয়ে ব্যথা শুরু হয়ে শেষে প্রচÐ রূপ নেয়, তেমন। এ রকম দিনগুলো গ্রামের মানুষ বর্ষাকালের মতো হেসেখেলে কাটায় না। তারা নতুন ফসল বোনার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতির সকল বৈরিতার সঙ্গে কোলাকুলি করে তারা ভবিষ্যতের স্বপ্নে বুক বাঁধে। তেমনই এক কর্মমুখর দিন আজ। মাঠে মাঠে নানা কাজের মধ্যে ডুব মেরে রয়েছে কৃষকরা। বাড়ির সামনে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। শান্টুর মা সেদিকেই তাকিয়ে ছিলো এতোক্ষণ। ধীরে ধীরে রোদ বাড়ছে। দুপুর হয়ে এলো তবু শান্টুর খোঁজ নেই। সেই যে ঘুম থেকে উঠে একমুঠো পান্তা ভাত আর একটা চম্পা কলা খেয়ে বেরোলো, বাড়ি ফেরার আর কোনো তাড়া নেই। ইদানিং কই যে থাকে ছেলেটা! স্কুলেও যাচ্ছে না ঠিকমতো। কী করছে, কোথায় যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। খুব যে খেয়াল রাখতে পারছে, তা না। তবু শান্টুর মা খুব বিরক্ত। শান্টুকে নিয়ে কতো হাউশ ওর বাবার। ও কি বাবার আশা পূরণ করবে না? তার খুব ভয় হয়, যা দিনকাল এখন! নেশাটেশায় আবার মজে যায় কি না! শান্টুর মা ইসমতারা মনে মনে আল্লার কাছে প্রার্থনা করে যেনো তার ছেলেটাকে তিনি ভালো রাখেন।
আজ আসুক শান্টুটা। আচ্ছা করে ধুলাই দিতে হবে। ইসমতারা মনে মনে ফুঁসতে থাকে। ঘর থেকে খুকখুক খুকখুক- একটানা কাশির শব্দ তেড়ে আসে, বিরতি দিয়ে। বিরক্তি লাগে। তবু শান্টুর মা প্রায় দৌড়ে যায় তার কাছে। শান্টুর বাবা খুব অসহায়। ইসমতারার সাহায্য ছাড়া সে এক মুহুর্ত চলতে পারে না। ইসমতারা সেটা বোঝে। তাই বিরক্ত হলেও সাড়া দিতে দেরি করে না। যেতে যেতেই হাঁক পড়ে। প্রায় অস্পষ্ট অথচ জোরকণ্ঠে- কই গো, শুইন্যা যাও। পানি খামু একটু।
ইসমতারা প্লাস্টিক জগ থেকে পানি ঢেলে গøাস তুলে দেয় তার হাতে। ঢকঢক করে পানি গিলে ফেলে সে। একটু শান্ত হয়ে, একটু থেমে তারপর জানতে চায়-
আইচ্ছা, পেলাডা কি মানুষ অইতো না, কিগো শান্টুর মা? সারাদিন কই ঘুইরা বেড়ায়? কথা কও না কেরে? একটু শাসন-টাসন করতে পারো না? অত লাই দেও কেরে? আমারেও আল্লা লুলা বানাইছে। নাইলে দেখতা, হের ভন্ডামিগিরি আমি ভাইঙ্গা দিতাম।
ইসমতারা কথা বলে না। সে জানে, এসব কথার উত্তর দেয়ার কোনো মানে হয় না। একবার উত্তর দিলে হাজারটা প্রশ্ন তৈরি হবে আবার। প্রশ্নের শেষ নেই। প্রশ্ন করতে করতে একসময় নিজেই সে থামবে। বিছানায় শুয়ে নাক ডেকে ঘুমিয়ে পড়বে।
ইসমতারা তরকারি কুটতে বসলো। দুপুরের রান্না করতে হবে। সকালে পেট ভরে খায়নি ছেলেটা। দুপুরে এসে খাবে তো। একবার ভাবে, আইজ আসুুক, দাও দিয়া কাইট্টা ফালামু। আাবার ভাবে, ইশ, খিদাও লাগে না পোলাডার? কী কষ্ট না জানি করতাছে ঘুইরা ঘুইরা। কয়ডা ভাত খায়া যাইতো…
রোদ আরও কড়া হয়ে ওঠে। যেনো চিক্কইর দেয়- এমন তেজ। তরকারি কুটতে কুটতে ইসমতারা ছেলের ভাবনা থেকে নিজের জীবনের ভাবনায় ঢুকে পড়ে। ভাবে, এমন কপালও হয় মানুষের? এমন পোড়া কপাল! বিয়ে হবার পর ভালোই চলছিলো সব। তিনবেলা খাওন, বছরে তিন-চারটা কাপড় আর একজোড়া জুতা। আর একটা সন্তান। এইসব চাহিদার বাইরে আর তো জীবন নেই তাদের। সব ঠিকঠাক ছিলো। শান্টুর বাপ রিকশা চালাতো। এ থেকে সংসার চালিয়েও কিছু টাকা সঞ্চয় করা যেতো। কিন্তু একদিন এক অভাগা দুপুরে দানব ট্রাক ধাক্কা দিলে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয় শান্টুর বাবা। একটা হাত আর একটা পা কেটে ফেলে দিতে হলো। ভাঙা রিকশাটা বিক্রি করে আর জমানো টাকায় চিকিৎসা চলেছে তার। শান্টুর বাবা ভেবেছিলো ছেলে লেখাপড়া করে অনেক বড় হবে। তাকে যেনো অটো-রিকশা চালানোর মতো কাজে আসতে না হয়। গাধার মতো জীবনের ঘানি টানতে না হয়। বিন্তু কে জানে, নিয়তি কার সঙ্গে কী খেলা করে? শান্টুটার কি লেখাপড়ো হবে আদৌ?
ভাবতে ভাবতে ইনমতারা উদাস হয়। হঠাৎ একদল ছেলেমেয়ের হৈচৈয়ে উদাসিনতার ঘোর কাটে তার। সে দৌড়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে একজনকে চিনে ফেলে সে, রাতুল। শান্টুন ক্লাসমেট। আগে মাঝেমাঝে আসতো বাড়িতে। একসাথে স্কুলে যেতো দুজন। কিন্তু মাঝখানে কী নিয়ে যে কথা কাটাকাটি হলো, আর আসে না। ইসমতারা জটলার ভেতর ঢুকে রাতুলকে টেনে বের করে নিয়ে আসে খোলা জায়গায়। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে জানতে চায় ছেলের কথা। কিন্তু রাতুল কিছু বলতে পারে না। উল্টো সে অবাক হয়, শান্টু কেনো ক’দিন ধরে স্কুলে যায় না। এ প্রশ্নের উত্তরে শান্টুর মা কিছু বলতে পারে না। রাতুলকে ছেড়ে সে আরেকটু সামনে এগোয়। পথের শেষ মাথা পর্যন্ত দেখে, শান্টুর ছায়াও নেই। ইসমতারা ব্যর্থ হয়ে নিজের উঠোনে ফিরে আসে। ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাসকে গোলপোস্ট থেকে বের আনা বলের মতো বাইরে ছুঁড়ে মারে। ছেড়াডা আর শান্তি দিলো না- বলতে বলতে কেটে ফেলা তরকারি নিয়ে রান্নায় ব্যস্ত হয় সে।
খুকখুক খুকখুক শব্দটা আবার আক্রমন করে। কাশিটা বাড়ছে। না বাড়ার অবশ্য কোনো কারণ নেই। ডাক্তার বারবার পান-বিড়ি খেতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। নিষেধ সে মেনে নিয়েছিলো ভালোভাবেই। কিন্তু মেয়াদ ছিলো সাতদিন। তারপর আগের মতোন। অভ্যাসের গরু, ঘাস তো খাবেই। প্রথম দুয়েকদিন বলে ইসমতারাও তেমন কিছু বলার জোর পায় না। একটা অচল মানুষের প্রতি এতোটা কঠোর আসলে হওয়া যায় না। মায়া লাগে। জীবনের সব আনন্দই তো মাটি হলো তার। এখন তার নিজের কাজ বলতে ওই একটাই- কাশতে থাকা আর সিগারেট টানা। এরমধ্যেই যেনো সে একটুখানি আনন্দ সন্ধান করে। আর সন্ধান করে ইসমতারার আন্তরিক স্পর্শের মধ্যে। আরেকটা উৎস তার আছে, শান্টু। কিন্তু ওখানে এখন আর তেমন ভরসা পাওয়া যায় না। বরং নিরাশার মেঘে আকাশ কেমন কালো হয়ে আসছে। ঝড়-তুফানে কবে সব ভেঙে তছনছ করে দেয়! এসব কারণেই ইসমতারা সিগারেটে বাধা দেয় না। বাধা যেটুকু দেয় তা হলো শরীরী স্পর্শের। ছেলে বড় হয়েছে। তাছাড়া জটিল জীবন তাড়া করতে করতে দেহের উদ্দামতাও নষ্ট হয়েছে। ভালো লাগে না। শান্টুর বাবার কামুকতার কাছে তবু মাঝেমাঝে তাকে হার মানতে হয়। মানুষটাকে উজ্জীবিত রাখার দায়িত্বও তো তারই। কিন্তু ইদানিং কাশিটা বেড়ে যাওয়া নিয়ে ইসমতারা ধমকায়। শান্টুর বাবা কিছু বলে না। আরো একটা কারণে চিন্তায় পড়েছে ইসমতারা। কাটা ঘা’টায় প্রচন্ড চুলকানিতে মাঝেমাঝেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে সে। রীিিতমতো চিৎকার করতে থাকে। দুদিন ধরে চুলকানি শেষে রক্ত পড়তেও দেখা যাচ্ছে। দেখে লক্ষণ খারাপ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ডাক্তার যে দেখাবে, সে উপায়ও নেই। টাকা থাকতে হবে তো!
ইসমতারা একটা দোকান চালায় নিজের ঘরে। সে দোকানের লাভের টাকাতেই সংসার চলে। চলেও কি বলা যায়? ঠেলেঠুলে চালাতে হয়। কিন্তু এরমধ্যেও ছেলেকে পড়াশোনা করাতে চায়। ওকে নিয়েই যতো চিন্তা। কিন্তু ও নিজে লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা করে না। ওকে দোষই বা দেয়া যায় কী করে! সংসারের এমন অনটনের মধ্যে লেখাপড়াও যে ঠিকমতো করা যায় না, সেটা ইসমতারা বোঝে। কিইবা করার আছে তার। ইসমতারার পক্ষে সব কিছু সামলানো কি এতো সহজ?
ইসমতারা নতুন একটা রাস্তা পেয়েছে। পাশের বাড়ির দিলারা তাকে এ খোঁজটা দিয়েছে। অদূরেই একটা ইটভাটা নির্মাণের কাজ চলছে। ওখানে কাজের জন্য অনেক লোক লাগবে। মহিলারাও কাজ করতে পারবে। সে কাজ নেবে ওখানে। দিলারার ভাই ইটভাটার কাজ করে। তাকে সে বলে রেখেছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই ইট বানানোর কাজ শুরু হবে। অবশ্য এ কাজ পাওয়ার জন্য দিলারলার ভাইকে দুই হাজার টাকা দিতে হবে। দেবে সে। কী আর করা! এ ব্যাপারে অবশ্য শান্টুর বাবাকে বলেনি সে।
দোকান নিয়ে এখন আর তেমন ভাবে না সে। মালামাল বিক্রি করে দুই হাজার টাকা হাতে জমাবে সে। ইটভাটায় কাজ করে স্বামী-সন্তানেরর মুখে তিনবেলা গরমগরম ভাত তুলে দেবে। স্বামীকে আরও দামি সিগারেট কিনে দেবে। ছেলেকে ভালো জামা কিনে দেবে। চিনিচাম্পার বদলে সবরি কলা কিনে দেবে। এসব ভাবনার ভেতর দিয়েই রান্না শেষ করে ইসসমতারা। এখন সে গোসলে যাবে। গোসল সেরে স্বামীকে খাওয়াবে। ছেলেটিও যেনো এরই মধ্যে ফিরে আসে। মনে মনে খুব আশা করে সে।
সন্ধ্যার ছায়া যখন লোভী বেড়ালের মতোন গ্রামের সবার ঘরে ঘরে উঁকি দিতে শুরু করেছে, তখন শান্টুর ছায়া বাড়ির উঠোনে পড়ে। সেও ঢোকে বেড়ালের মতোই প্রায় নিঃশব্দে। হাত-পা, কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে আছে। গায়ের চামড়া পুড়ে গেছে। চোখে মুখে তবু সজীবতার ভাব ধরে রেখে সে ঘরে প্রবেশ করে। ইসমতারা রেগে ছিলো আগে থেকেই। সারাদিন খোঁজ নেই, স্কুুলে যায় না, কোথায় বনে বাদারে ঘুরে বেড়ায়, খায় না, চেহারার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ভাত রান্না করে বসে আছে দুপুর থেকে। ছেলের অপেক্ষায় নিজের পেটেও ভাতের দানা পড়েনি। আবার দাঁত বের করে কেমন হাসছে। নির্লজ্জ একটা। ইসমতারা বকছে মনে মনে। শান্টুর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মা খুব রেগে আছে। তবে মার রাগ এমনই। শান্টুকে সামনে পেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব পানি। আজও সেরকমই হবে। তাই সে নির্ভয়ে আকুতি জানায়-
মা, ও মা এমন কইরা আছো ক্যান্? ইসমতারা প্রস্তুত ছিলো। রাগ পড়ছে না কিছুতেই। সে সবেগে উঠে এসে ধরাম ধরাম মারতে মারতে থাকে শান্টুকে। শান্টু বুঝতে পারে না। মায়ের এমন আচরণে অভ্যস্ত নয় সে। মার খেতে খেতে সে কেবল মা মা বলে চিৎকার করতে থাকে। মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ইসমতারা। তারপর রেগেমেগে কেঁদে ফেলে সে। চিৎকার করে বলে,
- কী অইছে, না? বাদাইম্যার গরের বাদাইম্যা, সারাদির তরে খুঁইজ্জা পাওয়া যায় না। খাওন দাওন নাই, ইস্কুল নাই। কই থাহস খবর নাই। যা তুই আমার সামনে থেইকা। তর মতন পোলা আমার দরকার নাই। যা।
ম্রা খেতে খেতে বসে পড়েছিলো শান্টু। এবার উঠে দাঁড়ায়। সবকিছু দেখেশুনে সে মার খাওয়াকে নিয়তি বলেই মেনে নেয়। মার দিকে আর একবারও তাকায় না। ক্ষুধার কথা ভুলে যায়। প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।
ইসমতারার স্বাভাবিক হতে সময় লাগে। ছেলেটা সত্যিই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। প্রায় পেছন পেছন সেও তাড়াহুড়ো করে বের হয়। শান্টু, শান্টু রে, বাপ কই তুই? যাইস না বাজান। হুন, আমার ভুল হইছে। বাজান রে! বলতে বলতে সে এগিয়ে যায় অনেকটা রাস্তা। কিন্তু শান্টুকে সে আর খুঁজে পায় না। কোথায় গেলো ছেলেটা?
ইসমতারা আবার ঘরের দিকে ফিরে আসে। ঘরের ভেতর চিল্লায় শান্টুর বাবা, - পোলাডারে মাইরা শেষ কইরা ফালতাছে। এইভাবে কেউ পোলাপাইনরে মারে, হেহ্!
ইসমতারা চুপচাপ বসে পড়ে ঘরের চৌকাঠে। বুকের ভেতরটায় তোলপাড় হতে থাকে। সত্যিই তো, আগে ছেলেটাকে খেতে দিতে পারতো। তারপর না হয় জিজ্ঞেস করা যেতো সে কোথায় যায়, কেনো যায়। নিজের ছেলেটাকে এভাবে মারলো কেনো সে। এখন কোথায় খুঁজবে?
ভাবতে ভাবতে বুক ভেঙে কান্না আসে ইসমতারার। সে টর্চলাইট নিয়ে বাইরে বের হয়। কোথায় কোথায় যেতে পারে, ধারণা করতে করতে সবার বাড়িতে খোঁজ নেয়। বিশেষ করে ওর বন্ধু বশির, সজন, বাপ্পি- সব বন্ধুর বাড়িতে। কোথাও নেই। এখন কী করবে সে? বড় দুশ্চিন্তা হতে থাকে ইসমতারার। প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুরেও ছেলের কোনো খোঁজ না পেয়ে তার ভয় বাড়তে থাকে। নানা চিন্তা মাথায় ভর করে তাকে পাগল করে তোলে। ছেলেটা অন্য কিছু করে বসবে না তো? গতবছর এমন এক খারাপ ঘটনা ঘটেছিলো নয়নপাড়া গ্রামে। পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করেছিলো বলে মা বকেছিলো ছেলেকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছেলেকে ঘরে পাওয়া যায় না। খুঁজে পাওয়া গেলো বাড়ির পেছনে ঝুলন্ত অবস্থায়। কী সুন্দর ছিলো ছেলেটা!
বাড়িতে ফিরে পেছনের ঝোপটাতে খোঁজ করে সে। না, নেই। ইসমতরার মন খুব উতলা আর বিক্ষিপ্ত। ভাঙা মন নিয়ে ঘরে ঢুকতেই শান্টুর বাবার গলা। সেও চিন্তায় আছে।
-কই, আনছো পেলারে? কথা কও না কেরে, আনছো? ও শান্টুর মা, কথা কও না কেরে?
ইসমতারা কথা বলে না। কী বলবে সে! আবার চিল্লায় শান্টুর বাবা,
- পোলায় আমার সারাদিন খায়নাই। কই, পাইছো নাকি খুইজ্জা?
ইসমতারা এবারও কথা বলে না। এক অজানা শংকা তাকে ঘিরে ধরে। কোনো সাড়া না পেয়ে হঠাৎ রোদন করে ওঠে শান্টুর বাবা, - সব আমার কফাল। আল্লায় আমারে লুলা বানাই দিছে। এর থাইক্কা বালা আছিন দুইন্নাইত্যে উডায়া নিলে। খোদা, কতো মাইনষেরে তুমি উপ্রে উডায়া নিছো, আমারে কেরে নিচে ফালায়া রাখছো? আমারে নেওগা খোদা!
শান্টু বিল্লালের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়।
- বিল্লাল ভাই, ও বিল্লাল ভাই, উডো না!
বিল্লালের উঠতে সময় লাগে। মহর আলী ব্রিকসের ম্যানেজারের সহকারি সে। ইটভাটার পাশে একটা ঘরে থাকে। দুনিয়াতে সে একা মানুষ। একাকিত্ব কাটানোর আশায় বিয়ে করলে বউটাও মরে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। অদূরেই অবশ্য কামলাদের কয়েকটি পরিবার থাকে। চোখ মুখ কচলে দরজা খুলতে খুলতে জানতে চায় সে, - কেডা? অত রাইতে জ্বালাইতে আইছস?
- আমি, বিল্লাল ভাই, শান্টু।
- অত রাইতে? এইহানো কেরে তুই?
- রাইত কই বিল্লাল ভাই, মাত্র তো নয়টা বাজদাছে। আইচ্চা, দরজা খোলো।
- খুলতাছি। বলতে বলতে দরজা খোলে বিল্লাল।
শান্টু ডাকের অপেক্ষা না করে ঘরে ঢুকে চৌকির এক কোনায় বসে পড়ে। বসেই জিজ্ঞেস করে সে, - বিল্লাল ভাই, ভাত আছে?
বিল্লাল অবাক হয়। শান্টুর চোখ-মুখ শুকনা। সে তো বাড়িছাড়া থাকেনি কখনো। ভাতের কথা জিজ্ঞেস করায় মনে পড়লো ডেকচিতে অল্প ভাত পড়ে আছে। কিন্তু তরকারি তো সবটাই খেয়ে ফেলেছে সে। বিল্লাল বলে, - দেখ, আছে দুই মুঠ। তর তো পেট ভরতো না রে ভাই। তরকারিও নাই। খাইবি কেমনে?
- তরকারি লাগদো না। খাইতে পারুম।
বলে সে ডেকচি থেকে থালায় ভাত নেয়। ডেকচির মুখের উল্টানো সরায় সে একটা কাচা মরিচও পেয়ে যায়। সাথে একটু লবণ মিশিয়ে খেতে শুরু করে সে। কিন্তু পরিমানে এতো কম যে, তিন লংকায় শেষ হয়ে যায়।
তরকারি ছাড়া ভাত খাওয়ার অভিজ্ঞতা কম নয় শান্টুর। বিশেষ করে বাবা অচল হওয়ার পরে বেশ কিছুদিন তরকারি ছাড়া, এমনকি দুই বেলা খেয়েও থেকেছে সে।
স্কুল ফাঁকি দিয়ে মহর আলী ইটভাটায় যোগালি হিসেবে কাজ করে শান্টু। বিল্লালের হাতেপায় ধরে সুযোগ পেয়েছে সে। বেশকিছু টাকা জমেছে। সেগুলোও বিল্লালের কাছেই। আর কিছু টাকা হলেই বাবার চিকিৎসা আর একটা হুইল চেয়ার কিনবে শান্টু। শান্টু খেয়াল করেছে, ঘরে শুয়েবসে থাকতে থাকতে বাবা মানসিকভাবে বেশি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তার একটু বাইরে বেরোনো দরকার। মানুষের সাখে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। তাতে মনমেজাজ ভালো হবে। প্রয়োজনীয় টাকাটা যোগাড় হতে আরও দিনদশেক কাজ করতে হবে শান্টুকে। কিন্তু এতোদিন ধৈর্য কুলাবে না তার। বিশেষ করে স্কুলে না যাওয়া নিয়ে মা বাবা খুব চিন্তিত। এ রহস্যৗটাও দীর্ঘমেয়াদী হতে দেওয়া ক্ষতিকর হবে, ভাবে শান্টু। ভেবে অস্থির লাগে। এ অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিতে পারে কেবল বিল্লাল ভাই। সে হুট করেই বিল্লালের পায় ধরে বসে। সে দশদিনের মজুরি অগ্রিম পেতে চায়। এটা তার লাগবেই। ম্যানেজারকে বলে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বিল্লাল রাজি হয় না। সে ‘দয়ায় আপদ বাড়ে’ বিষয়ক প্রবাদটা মনে মনে আওড়ায়। কিন্তু শান্টু নাছোড়বান্দা। টাকা তার লাগবেই। প্রয়োজনে সে দুদিন বেশি কাজ করে দেবে।
সকালবেলা শান্টুর বাপকে এককাপ চা আর দুটো টোস্ট বিস্কুট খেতে দিয়েছিলো ইসমতারা। আর কিছু না। এখন দুপুর। ইসমতারা কিছুই খায়নি। রান্না করেনি। শান্টুর বাবার কাশিটা বেড়েছে। সিগারেট টানাটাও। সে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে চালের দিকে টানানো ময়লা সামিয়ানার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানে মাকড়শা জাল বোনে। টিকটিকি দৌড়ে পালায়। সে ভাবে ধুর! মাকড়শা হলেও মন্দ কী ছিলো? কিংবা টিকটিকি হলে? জীবন এতো জটিল আর কঠিন হতো না।
কিন্তু ঠাঠা দুপুরের ভেতর ঘেমেনেয়ে একটা অটো নিয়ে শান্টু সরাসরি বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করলে শান্টুর মা দেখে বিশ্বাস করতে চায় না। চালকের সহযোগিতায় শান্টু প্রথমে হুইল চেয়ারটা নামায়। তারপর চালের বস্তা আর তারপর একটা জ্যান্ত দেশি মুরগি যার কক কক ডাকটা শান্টুর বাবার কান অবািধ পৌঁছে গিয়ে একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। তার কান খাড়া হয়। সে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু পারে না বলে শান্টুর মাকে গলা তুলে ডাকে। শান্টুর মা সাড়া দিতে পারে না। সে দৌড়ে গিয়ে শান্টুকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদতে শুরু করে। এই কান্না দীর্ঘমেয়াদী হলে অটোচালক একটা গলা খাকড়ি দিয়ে তার ভাড়া চায়। শান্টু ভাড়া দিয়ে তাকে বিদায় করে মার সাথে ঘরে ঢোকে। শান্টু বাবার জন্য একটা নতুন লুঙ্গি আর একটা সাদা বেনিয়ান গেঞ্জি, মার জন্য একটা ছাপা শাড়িও কিনে এনেছে। লুঙ্গি আর গেঞ্জি নিয়ে বাবার সামনে গেলে বাবা কান্না সামলাতে পারে না। নিজের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে ফুঁপিয়ে ওঠে। শান্টু বাবাকে জড়িয়ে ধরে। বুঝ হবার পর সম্ভবত এই প্রথম সে বাবাকে জড়িয়ে ধরতে পারলো। তারপর লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরিয়ে যখন তাকে হুইল চেয়ারে তুলে দিলো, তখন আরেক প্রস্ত কান্না তাকে ভাসিয়ে দিলো। এ কান্না দুখের না সুখের, এর ব্যাখ্যা সহজ করে দেয়া যায় না।
চেয়ার ঠেলে তাকে বারান্দায় নিয়ে আসা হলো। মাকে শান্টু বললো শাড়ি পরে আসতে। ইসমতারা শাড়ি পরে এসে দাঁড়ালো স্বামীর পেছনে। তিনজনের মুখেই ফুলের মতো হাসি ফুটলো। দুপুরের প্রচÐ রোদও তাদের সে সম্মিলিত হাসিকে ¤øান করতে পারলো না। শান্টু একটা ক্যামেরাওয়ালা মোবাইলের অভাব বোধ করলো। এমন একটা মোবাইল থাকলে আজকে তাদের সংসারের সবচে সুন্দর ছবিটা তুলে রাখা যেতো। মোবাইল সে কিনতেই পারতো। কিন্তু তার হাতে যে টাকাটা আছে এখন, এটা বাবার চিকিৎসার জন্য।
রোদের তাপটা আরাম দিচ্ছে না। তাদের তাই ঘরে ঢুকতে হলো। ঘরে ঢুকেই শান্টু তার মায়ের হাতে টাকাটা তুলে দিলো। সাত হাজার। টাকা হাতে নিয়ে মা আবার কাঁদে। ছেলের মুখে চুমু খায়। শান্টুর বাবা চেঁচায়, অ্যাই, আবার কান্দো কেরে? কী হইছে?
ইসমতারা জবাব দেয় না। ছেলেকে এক বাটি মুড়ি দিয়ে সে রান্নায় ব্যস্ত হয়। ছেলে মুড়ির বাটি নিয়ে বাবার কাছে যায়। দুজনে ভাগাভাগি করে খায়। ইসমতারা রান্না করে আর কাঁদে। তার রান্না এবং কান্না ফুরায় না। একদিনেরও কম সময়, তবু তার মনে হয়, কতোদিন ছেলে না খেয়ে আছে। কতোদিন ছেলেকে সে রান্না করে খাওয়ায় না।
বিকেলে হুইলচেয়ার ঠেলে ঠেলে বাড়ির সামনে আসে শান্টুর বাবা। অনেকের সাথে দেখা হয়। একটু সামনে এগোলে দোকানদার ছোবান মিয়া তাকে এককাপ চা খেতে দেয়। আরেকজন দেয় একটা বনরুটি। সে আরাম করে খায়। নানান কথা চলে। শান্টুর বাবার অনেক কথা জমা ছিলো। তাই সে যেনো সবারচে একটু বেশিই বলে। সে আরেকটু এগিয়ে মসজিদের সামনে যায়। এলাকায় বিদেশি টাকায় নতুন মসজিদ হয়েছে। মুসল্লি বেড়েছে মসজিদে। মানুষের হাতে টাকাও হয়েছে। মোলায়েম হাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেলো। আনন্দে চিকিচিক করে উঠলো তার চোখজোড়া।
এখন থেকে প্রতি শুক্রবারে সে মসজিদে আসবে। দ্বীন এবং দুনিয়া- দুটোরই কাজ হবে। শান্টুকে বলতে হবে যেনো নতুন একটা গামছাও কিনে দেয়। কাঁধে করে নিয়ে আসবে। নামাজশেষে মেলে ধরবে, ব্যাস! হুইলচেয়ারটা কিনে দেয়ায় ছেলের প্রতি মনেমনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে। সে নিজের প্রতি আত্ববিশ্বাস ফিরে পেতে থাকে।
শান্টু আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করে, যে বাবা-মা স্কুলে না যাওয়া নিয়ে এতো গালাগাল করতো, তারা এখন এ নিয়ে টু শব্দটিও করছে না। অভাবের সংসারে সামান্য বেশি টাকার গন্ধ তাদেরও কি মাতাল করে দিয়েছে, যেমনটা করেছে শান্টুকে? শান্টু স্থির সিদ্ধান্ত নেয়। সে আর স্কুলে যাবে না। সে শুধু টাকা কামাবে। জীবনে টাকার যে কী প্রয়োজন, সে ভালোভাবে বুঝে গেছে। টাকা জীবনে অনেককিছুর ঘাটতি পুষিয়ে দেয়।
ইটভাটার পাশ দিয়ে যখন তার সহপাঠিরা স্কুলে যায়, শান্টু তাদের দেখতে পেয়ে বিষাদাক্রান্ত হয়। কিছু সময়ের জন্য কষ্টের মেঘ জমে তার মনের আকাশে। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবে, তাদের তো শুধু পড়া আর পড়া- বিরক্তিকর। তারা কি শান্টুর মতো কড়কড়ে টাকা পায়? টাকার গন্ধ যে কী ঝাঁঝালো, তারা সেটা জানে? টাকার গন্ধ তাকে এতো আকর্ষণ করেছে যে বইয়ের গন্ধ আর টানে না একদমই। শান্টুর মনে হয় সে বড় হয়ে গেছে। মনে হয় যে, সে সহপাঠিদেরচে দশ বছর বেশি বয়সের। তাদেরচে দশগুণ বেশি দায়িত্বশীল। ভেবে আনন্দ লাগে।
তার ইটভাটার মালিকের পড়াশোনা নেই। কিন্তু বিভিন্ন মিটিংয়ে যায় স্যুট-বুট পরে। বাবুসাব হয়ে। লোকজন তাকে সালাম দেয়, আবার সমীহও করে। শান্টু মনেমনে ভাবে, যদি সে বিশ বছর পরিশ্রম করে আর টাকা জমায়, তাহলে তার পক্ষেও একদিন এমন একটা ইটভাটার মালিক হয়ে পড়া অসম্ভব নয়। তখন সে স্যুট-বুট পরে ঘুরে কেড়াবে, মিটিংয়ে যাবে, মানুষকে দান-খয়রাত করবে। লোকজন তাকে সালাম দেবে, সমীহ করবে। ভেবে খুব আনন্দ লাগে শান্টুর।
ইসমতারা ইটভাটার কাজটা পেয়ে গেছে। দুই হাজারের কথা থাকলেও তিন হাজার দিতে হয়েছে। তবে তার একটা সুবিধা হয়েছে, সে দুপুরে কাজে গিয়ে রাত ৮টায় ফিরে আসতে পারবে। পরিবার সামলাতে আর কোনো কষ্ট হবে না তাতে। খুব খুশি ইসমতারা। তার সংসারে আর অভাব থাকবে না। চিকিৎসার সাত হাজার থেকেই এ টাকা বের করে দিয়েছে সে। সে ভাবছে, দুয়েক মাস পরে স্বামীর চিকিৎসা করালে তেমন ক্ষতি হবে না। তাছাড়া দোকানের মালামাল বিক্রি হলে এ থেকেও কিছু টাকা আসবে।
শান্টুর বাবা শুক্রবারে নিয়মিত নামাজে যেতে শুরু করেছে। বউয়ের কাছে সিগারেটের টাকা চায় না। পায়ের ঘাঁ নিয়েও আর কথা বলে না। একটা হইলচেয়ার তার জীবনকে অনেক স্বস্তিদায়ক করে তুলেছে। তার আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে। ভেবে ইসমতারাও কিছুটা নির্ভার হয়।